অযোধ্যা, ধর্মনিরপেক্ষতা আর ভারতের রাজনীতির কাহিনি

জয়ন্ত ঘোষাল
জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দেশের মুখ্যমন্ত্রীদের মাসে দু’টি করে চিঠি দেওয়ার একটি প্রথা চালু করেছিলেন। এই প্রথা অনুসারে মাসের ১৫ তারিখে নেহরু একটি চিঠি দিতেন। মুখ্যমন্ত্রীদের সেই চিঠির জবাব দিতে বলতেন। তারপর মাসের শেষে আর-একটি চিঠি দিতেন। নেহরু বলেছিলেন, এর মানে এই নয়, আপনারা মাসে দু’টির বেশি চিঠি দেবেন না, বা শুধুই চিঠির উত্তরটুকু দেবেন। আপনারা চাইলে যে-কোনও বিষয়ে চিঠি লিখতে পারেন আমাকে।

সেই সময়ে ফেসবুক, ট্যুইটার, ই-মেল বা সোশ্যাল মিডিয়ার বিচিত্র ব্যবস্থা ছিল না। ফলে চিঠিই ছিল কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় যোগসূত্র। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরে সে-বছরের ১৫ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীদের উদ্দেশে লেখা প্রথম চিঠিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেহরু লিখেছিলেন, ভারতীয় মুসলমানদের উন্নতি প্রয়োজন। উদাহরণ হিসাবে নেহরু সেই সময়ে জিন্নার একটি বক্তৃতার কথাও উল্লেখ করেন। যে-বক্তৃতায় জিন্না বলেছিলেন, পাকিস্তানের ভিতরে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের দিকটিও দেখতে হবে। যদি পাকিস্তানের ভিতরে ধর্মীয় সংহতি প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তা হলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হামলার আশঙ্কাও কমবে। জিন্নার ওই বক্তৃতার দৃষ্টান্ত দিয়ে নেহেরু মুখ্যমন্ত্রীদের বলেছিলেন, ভারতের সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মিলন প্রয়োজন। ভারতীয় মুসলমানরা ভারতীয়। কিন্তু মুসলমান সমাজকে তোষণ করার নীতি সম্পূর্ণ অর্বাচীনের কাজ। কোনও ধরনের তোষণ অথবা রাজনৈতিক দুর্বলতা প্রকাশের প্রশ্নই ওঠে না। নেহরুর আশঙ্কাই ছিল, সংখ্যালঘু-তোষণ করা হলে ভবিষ্যতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজেও প্রতিক্রিয়া শুরু হবে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠবাদ— সে-ও কিন্তু দেশের সংহতি এবং অখণ্ডতা রক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। (এখানে একটা কথা বলে নেওয়া ভালো, ‘৪৭ সালে নেহরু কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীদের ‘আমার প্রিয় প্রিমিয়ার’ বলে সম্বোধন করে চিঠি লিখতেন, কেননা তখনও তাঁরা ‘মুখ্যমন্ত্রী’ হননি, ১৯৫০ সালের পরে সাংবিধানিক ভাবে তাঁরা ‘মুখ্যমন্ত্রী’ হলেন)।

আজ যখন নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী, আর অমিত শাহ দলের একচ্ছত্র কর্তৃত্বে, যখন উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন থেকে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতি নিয়ে আমরা আলাপ-আলোচনা করছি, তখন নেহরুর লেখা এই প্রথম চিঠিটি পড়লে কিন্তু বিস্মিত হতে হয়! যে-নেহরু আরএসএস-এর কার্যকলাপকে হিটলারের ফ্যাসিবাদের সঙ্গে তুলনা করছেন, সেই নেহরু সংখ্যালঘুদের তোষণের বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। সঙ্ঘ-পরিবারের মতে, নেহরু বাস্তবে কিন্তু তোষণের নীতিকে বর্জন করেননি, বা চাইলেও বর্জন করতে পারেননি। কংগ্রেস ভারতে ৬০ বছরের বেশি সময় ধরে রাজত্ব করেছে। কাজেই নেহরু যে সংখ্যালঘু-তোষণকে ‘কমপ্লিট ননসেন্স’ বলেছেন সেটিকে কংগ্রেস নেতৃত্ব বাস্তবে যদি ‘ননসেন্স’-এ পরিণত করতে পারতেন, তা হলে হয়তো মুদ্রার অন্য পিঠ বিজেপি তথা সঙ্ঘ-পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি হত না।
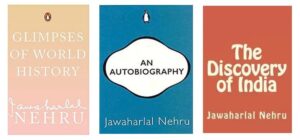
নেহরুর এই চিঠিগুলি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি পেঙ্গুইন ‘৪৭ থেকে ‘৬৩ সাল পর্যন্ত লেখা নেহরুর এই সমস্ত চিঠি থেকে নির্বাচিত একগুচ্ছ নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেছে। বইটির নাম ‘লেটারস্ ফর আ নেশন ফ্রম জওহরলাল নেহরু টু হিজ চিফ মিনিস্টারস্’। বইটি সম্পাদনার কাজ করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি গবেষক মাধব খোসলা। এই বইটির ভূমিকায় মাধব খোসলা বলেছেন, নেহরু যে-তিনটি বই লিখেছেন সেই তিনটিই কিন্তু স্বাধীনতার আগে। এবং জেলে বসে লেখা। প্রথম বই ‘গ্লিম্পসেস্ অব ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি’ (১৯৩৪)। এর পরে লেখা ‘একটি আত্মজীবনী’ (১৯৩৬) এবং ‘দ্য ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া’ (১৯৪৬)। সেই সময়ে নেহরুর ভাবনা-চিন্তা, মতাদর্শ, ভারত সম্পর্কে ধ্যানধারণা— সে-সব জানা যায় এই বইগুলি থেকে। কিন্তু স্বাধীনতার পরে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রশাসক নেহরুর অগ্রাধিকার এবং ভাবনা-চিন্তা বুঝতে গেলে একমাত্র আকর তাঁর চিঠি।

রামচন্দ্র গুহ বলেছেন— মজার ব্যাপার, নেহরুর লিখিত বইগুলির ক্রম খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, নেহরু আগে বিশ্ববীক্ষা অর্জন করেন, ভারত সম্পর্কে তাঁর মতামত বিকশিত হয়েছে শেষে। নেহরুর আগেই মারা গিয়েছেন বল্লভভাই প্যাটেল (১৯৫০)। পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন দলের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ১৯৫১ সালে। ‘৫২, ‘৫৭ এবং ‘৬২ সালের তিনটি লোকসভা নির্বাচনেই কংগ্রেস সর্বেসর্বা। দিল্লিতে নেহেরুর বিরুদ্ধে কার্যত কোনও বিরোধী দল ছিল না। সমাজতন্ত্রী দল, কমিউনিস্ট পার্টি, ভারতীয় জনসঙ্ঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টি থাকলেও তারা নেহরুকে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারেনি। ‘৫৭ সালে কেরলে বিধানসভা নির্বাচনে কমিউনিস্টরা বিজয়ী হয় এবং সে-ই প্রথম একটা অকংগ্রেসি সরকার গঠিত হয়। কিন্তু পরে কমিউনিস্টরা গোটা দেশেই সে-ভাবে কিছু করে-উঠতে পারল না। উল্টে বিজেপি হিন্দু জাতীয়তাবাদকে এক নতুন চরিত্র দিল।
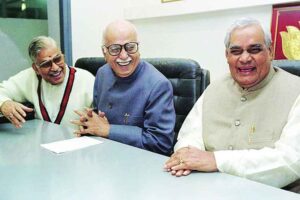
১৯৮০ সাল থেকেই হিন্দু জাতীয়তাবাদ এক নতুন চেহারা নেয়। ওই বছরে প্রতিষ্ঠার পর বিজেপি দ্রুত হিন্দুত্বকে একটা জাতীয় বিষয়ে পরিণত করতে তৎপর হয়ে ওঠে। ২০০১ সালের সেন্সাস অনুসারে ১০২ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৮০.৪৫ ভাগ ছিল হিন্দু। মুসলিম ছিল শতকরা হিসাবে ১৩.৪০ ভাগ। সম্প্রতি ‘রাউটলেজ হ্যান্ডবুক অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড পলিটিক্স’ গ্রন্থে হিন্দু জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত এক প্রবন্ধে গবেষক জেমস্ চিরিয়ানক্যান্ডাথ দেখিয়েছেন যে, ইন্দিরা গান্ধি তাঁর জনপ্রিয়তা রক্ষার জন্য যত বেশি করে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার শুরু করেন এবং তাতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সত্তাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন— গণমাধ্যমে তার প্রভাব পড়ে। উল্লেখ্য, ইন্দিরা গান্ধির সময়েই সারা ভারতে টেলিভিশন সম্প্রচার ছড়িয়ে পড়ে। এবং সেই সময়েই টেলিভিশনের মাধ্যমে একটা সমসত্ত্ব জাতীয় ধারণা হিসাবে হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমিলা থাপার বলেন, হিন্দু ধর্ম তখন আধুনিকীকরণের মতাদর্শ হয়ে উঠেছিল। রাজীব গান্ধির সময়ে, ১৯৮৭ এবং ‘৮৮-তে ‘রামায়ণ’ এবং ‘মহাভারত’ সিরিয়াল-দু’টি এই হিন্দু জাতীয়তাবাদকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এর ফলে ভারতীয় সমাজে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাও বাড়তে থাকে। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরেই তার ভয়াবহ পরিণতি দেখা যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। রামমন্দির আন্দোলন সেই মেরুকরণকে আরও তীব্র করে তোলে।
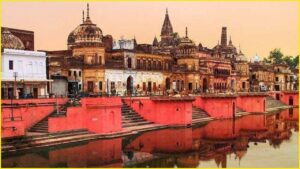
রাউটলেজ-এর আন্তর্জাতিক হ্যান্ডবুকে বলা হয়েছে, বিজেপি হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করলেও সেখানে ব্রাহ্মণদের দাপট ছিল বেশি। তাই বিজেপি কৌশল বদলে হিন্দু ধর্মকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে, ব্রাহ্মণ থেকে ওবিসি— নানা জাতের সমন্বয় সাধনে জোর দিয়েছে। এ-ই প্রথম নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটে।
বাজপেয়ী-জমানাতেও এনডিএ-কে শরিকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে এগোতে হয়েছিল। কিন্তু বিজেপি মনে করছে, হিন্দু জাতীয়তাবাদী প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এটাই সুবর্ণ সুযোগ।

সমস্যা হচ্ছে, ভারতে হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য বহুত্ববাদের মধ্যে নিহিত। আকবরের দীন-ই-ইলাহি থেকে সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যের সর্বধর্ম সমন্বয়ের মতাদর্শ ভারতীয় ঐতিহ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্যরা আসার আগেই ভারতীয় সভ্যতা ছিল বলে জানিয়েছেন ক্ষিতিমোহন সেনের মতো দার্শনিক। আর্যরা আসার পরে নানা সংমিশ্রণ হয়েছে। ভারতে রাজনৈতিক একদলীয় শাসন হলেও ভারতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ কিন্তু থেকেই গিয়েছে। তাই হিন্দু সত্তাকে একটি একক সত্তা হিসেবে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা কতটা সফল হবে সে-প্রশ্ন থেকেই যায়! বরং যদি সময়ের হাত ধরে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি বদলানো সম্ভব হয়, সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, তাতে হয়তো হিন্দু জাতীয়তাবাদের অস্তিত্ব সুরক্ষিত হবে।
জয়ন্ত ঘোষাল : বিশিষ্ট সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার।
ছবি ঋণ : ইন্টারনেট

Comments are closed.